বাংলাদেশ আজ এক নীরব কিন্তু ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—বনভূমি ধ্বংস। এ দেশের সামগ্রিক ভূখণ্ডের মাত্র ১৪.৫% বনভূমি, যা ইতিমধ্যেই পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রার নিচে। অথচ প্রতি বছর এই সামান্য বনভূমিও অব্যাহতভাবে হারিয়ে যাচ্ছে, যার ফলে দেশের জলবায়ু, কৃষি, জীববৈচিত্র্য এবং মানুষের জীবনমানের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ছে।
বনভূমি ধ্বংসের কারণ
১. কৃষি ও আবাসন সম্প্রসারণ: বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য ও আবাসনের চাহিদা মেটাতে প্রতিনিয়ত বনভূমি উজাড় করা হচ্ছে। সিলেট, মৌলভীবাজার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের টিলা ও পাহাড় কেটে তৈরি হচ্ছে চা বাগান, কৃষিজমি ও বসতি এলাকা।
২. শিল্পায়ন ও নগরায়ন: ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জসহ দেশের প্রধান শহরগুলোর বিস্তৃতি ঘটছে আশপাশের বনভূমি গ্রাস করে। রাস্তাঘাট, কারখানা, গুদামঘর তৈরির জন্য বনাঞ্চল উজাড় করা হচ্ছে।
৩. অবৈধ কাঠ সংগ্রহ ও ইটভাটা: ইটভাটা ও জ্বালানি কাঠের চাহিদা মেটাতে বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য জেলায় অবৈধভাবে গাছ কাটা অব্যাহত রয়েছে। বন আইনের প্রয়োগ দুর্বল হওয়ায় এই প্রবণতা বন্ধ হচ্ছে না।
৪. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর নির্ভরতা: দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠী বন থেকে কাঠ, মধু, ফলমূল, ওষধি গাছ সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে। অতিরিক্ত সংগ্রহের ফলে বনভূমি নিঃশেষ হয়ে পড়ছে।
৫. জলবায়ু পরিবর্তন: বৃষ্টিপাতের অনিয়মিত ধরণ, খরা ও উষ্ণতার কারণে বনভূমির স্বাভাবিক পুনর্জন্মের গতি কমে গেছে। এতে গাছের বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, মৃতপ্রায় হয়ে পড়ছে অনেক বনাঞ্চল।
প্রভাব
১. জীববৈচিত্র্যের অবক্ষয়: বনভূমি হারানোর ফলে বিপন্ন হচ্ছে বাঘ, হরিণ, বনমোরগসহ বহু প্রাণী। সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অসংখ্য পাখি ও কীটপতঙ্গ আজ বিপন্ন অবস্থায়।
২. ভূমিক্ষয় ও ভূমিধস: সিলেট, মৌলভীবাজার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ে অবৈধ বসতি স্থাপনের কারণে প্রতিবছর টিলা ধসের ঘটনা ঘটছে। ২০১৭ সালে রাঙামাটিতে পাহাড়ধসে ১২০ জনের প্রাণহানি হয়। বন উজাড়ের ফলে ভূমির স্থিতি নষ্ট হয়ে এ ধরনের দুর্যোগ বাড়ছে।
৩. জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব: বনভূমি কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে। বন কমে যাওয়ায় গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনত্ব বাড়ছে। এতে বৃষ্টির স্বাভাবিক চক্র ব্যাহত হচ্ছে, খরা ও বন্যার মাত্রা বাড়ছে।
৪. অর্থনৈতিক বিপর্যয়: বনজ সম্পদের স্বল্পতা ও পর্যটন শিল্পের ক্ষতি হচ্ছে। সুন্দরবনের পর্যটন সম্ভাবনা কমে যাচ্ছে। বনসম্পদের অভাব কৃষি ও মাছচাষেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।
৫. স্থানীয় জনগণের জীবিকা সংকট: বনজ সম্পদের ওপর নির্ভরশীল জাতিগোষ্ঠী আজ বিকল্প আয়ের পথ না পেয়ে দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাচ্ছে।
বন আইন ও ব্যবস্থাপনা
বাংলাদেশ বন আইন, ১৯২৭ অনুযায়ী সংরক্ষিত ও সংরক্ষণযোগ্য বনাঞ্চলে গাছ কাটা, জমি দখল, পশু চরানো নিষিদ্ধ। কিন্তু আইনের প্রয়োগ দুর্বল। বন অপরাধ দমন ইউনিট ও স্থানীয় বন কর্মকর্তাদের দুর্বল নজরদারি ও স্বচ্ছতার অভাবের কারণে নিয়মিত বন উজাড় চলছে। ২০০০ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন প্রণীত হলেও বাস্তবায়ন তেমন কার্যকর হয়নি।
প্রতিকার ও সুপারিশ
১. কঠোর আইন প্রয়োগ: বন আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করে অবৈধ দখল, চোরাকারবারিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।
২. বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি: সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে টেকসই বৃক্ষরোপণ ও বন পুনরুদ্ধার কর্মসূচি চালু করতে হবে।
৩. পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন: বনাঞ্চল ধ্বংস না করে পরিকল্পিত শিল্প এলাকা গড়ে তোলা প্রয়োজন।
৪. স্থানীয় জনগণের বিকল্প জীবিকা নিশ্চিতকরণ: পর্যটন, মাছচাষ, মৌচাষ, ওষধি গাছ চাষের মতো বিকল্প আয়ের উৎস তৈরি করতে হবে।
৫. সচেতনতা ও শিক্ষা: স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বন সংরক্ষণ বিষয়ে শিক্ষা চালু করতে হবে।
বিশেষজ্ঞ মতামত: ড. শামীম আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক বলেন: “বনভূমি ধ্বংসের হার কমাতে হলে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। বন রক্ষার সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িয়ে না দিলে এই সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়।”
আব্দুল হান্নান, রাঙ্গামাটির পরিবেশ গবেষক জানান: “পাহাড় কেটে বসতি ও কৃষিকাজ বন্ধ না করলে প্রতি বছরই নতুন ভূমিধসের ঝুঁকি থাকবে। বনভূমি ধ্বংস পাহাড় অঞ্চলের জন্য আত্মঘাতী।”
উপসংহার: বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে বনভূমি ধ্বংস বন্ধ করতেই হবে। আইন প্রয়োগ, সচেতনতা, স্থানীয় জনগণের বিকল্প আয় সৃষ্টি এবং পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন নিশ্চিত করা ছাড়া এই সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়। সময় এখনই—নইলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক বিপন্ন পরিবেশ রেখে যেতে হবে।
________________________________________
লেখক পরিচিতি: এস এম মেহেদী হাসান একজন স্বাধীন সাংবাদিক ও গবেষক, যিনি পরিবেশ, সামাজিক ও মানবাধিকার বিষয়ক লেখালেখির সাথে জড়িত।
মোবাইল: +৮৮০১৭১১৯৩৪৩৫৮ ই-মেইল: rumeenews@gmail.com
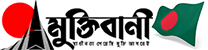

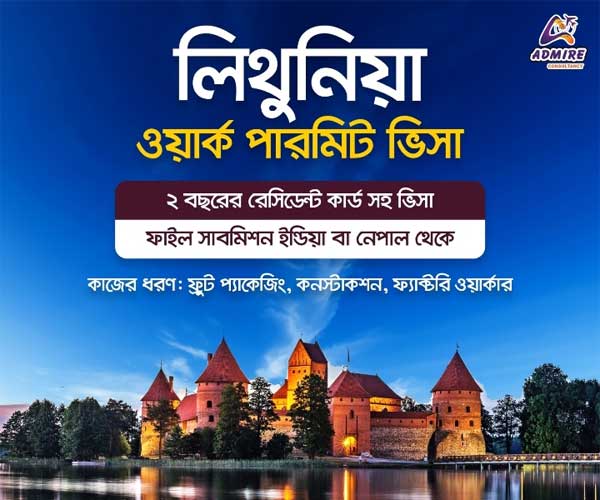




















পাঠকের মন্তব্য